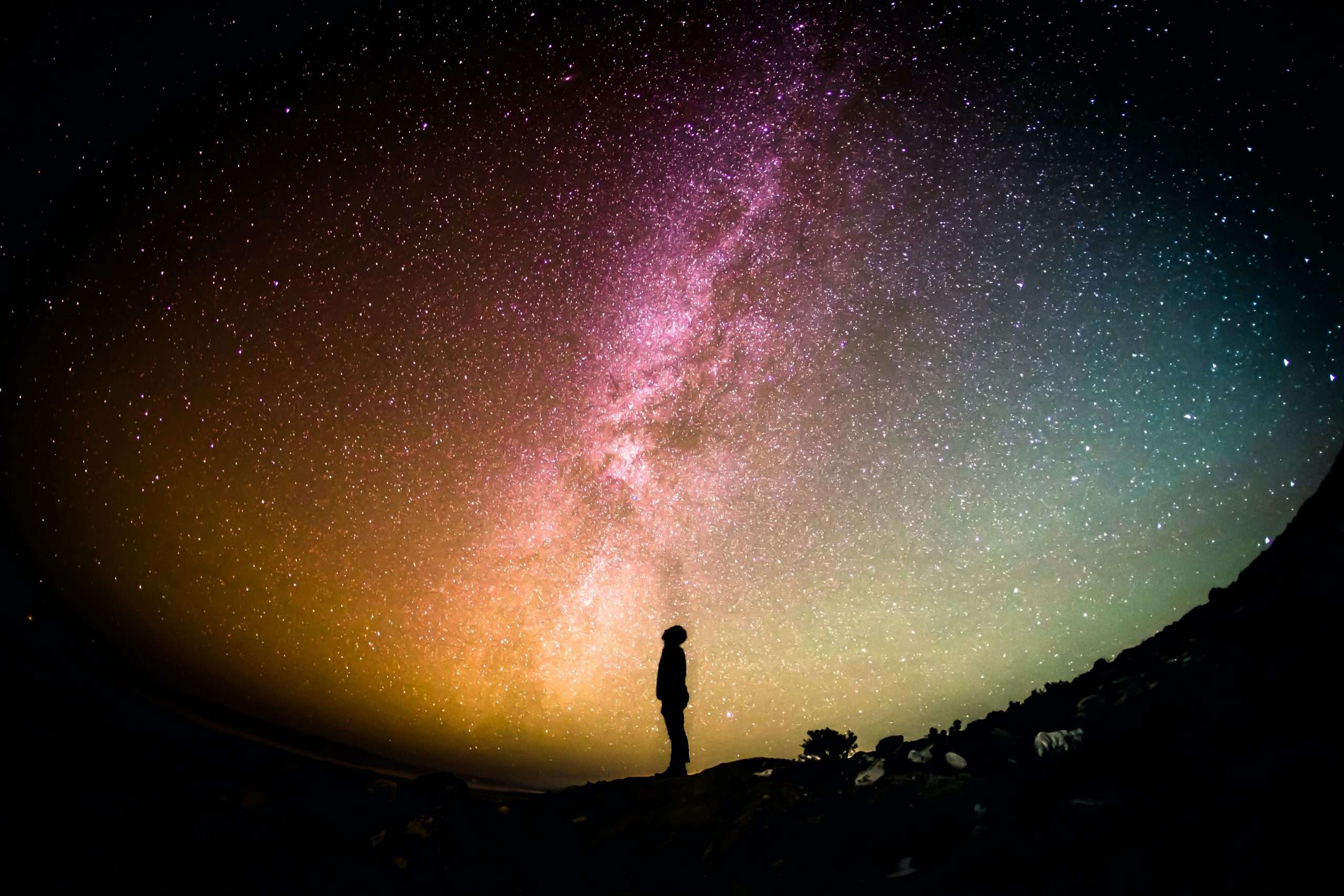
আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে নির্ভরশীলতার যুক্তি; Argument from contingency
আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে নির্ভরশীলতার যুক্তি (Argument from contingency).
মানব মনের স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন হলো এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে। মহাবিশ্বের উৎপত্তির পিছনে কি কোনো বুদ্ধিমান সত্তার হাত রয়েছে? আল্লাহর অস্তিত্ব কি সত্যিই আছে? দুনিয়ার এই জীবনই কি একমাত্র জীবন, নাকি এরপরেও কোন জীবন আছে? মৃত্যুর সাথে সাথেই কি এই জীবনের সমাপ্তি, নাকি এর পরেও পরকালের জীবনের জের টানতে হবে? মানব মনের স্বাভাবিক এসব প্রশ্নের জের ধরেই যুগে যুগে মানুষের মধ্যে নানারকম মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এসব প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রধানত দুটি বিপরীতমুখী মতবাদ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচিত। একটি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের পক্ষে এবং অন্যটি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের বিপক্ষে। স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে মানব ইতিহাসের শুরু থেকে বিতর্ক হয়ে আসছে এবং সম্ভবত এই বিতর্কের অবসান হয়তো কখনোই হবে না। আস্তিক এবং নাস্তিক উভয়ই এই বিষয়ে তাদের অবস্থানকে ন্যায্য করার জন্য স্ব স্ব যুক্তি, তথ্য উপস্থান করেছে। এই অংশে আমি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের পক্ষের কিছু যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।
এই যুক্তিটির মূল উপাদান হল একটি কার্যকারণ নীতি। যেমন, যা কিছু অস্তিত্বে ব্যর্থ হতে পারতো তার অস্তিত্বের জন্য একটি কারণ রয়েছে। প্রকৃতিতে আমাদের অভিজ্ঞতায় যা কিছুর মুখোমুখি হই তার সব কিছুর অস্তিত্ব ব্যর্থ হতে পারতো। যেমন, আপনার হাতে থাকা মোবাইল ফোন, ইট-পাথর, গাছ-পালা, কুকুর-বিড়াল, গ্রহ, তারা, ধূলিকণা ইত্যাদি; এই জিনিসগুলো অস্তিত্বে নাও থাকতে পারতো। আমরা খুব সহজেই এমন একটি মহাবিশ্ব কল্পনা করতে পারি যেখানে এগুলোর অস্তিত্ব নেই। এই জিনিসগুলো তার অস্তিত্বের জন্য কোনো-না-কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে কি, যা তার অস্তিত্বের জন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়? যার অস্তিত্বে থাকাটা অপরিহার্য? অপরিহার্য অস্তিত্ব বলতে বুঝাচ্ছি এমন কিছু যা সকল সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে বিদ্যমান বা অস্তিত্বশীল। যার অস্তিত্বহীনতা অসম্ভব। এই লিখাতে আমরা এমন একটি অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করবো যা তার অস্তিত্বের জন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, যার অস্তিত্ব থাকাটা অপরিহার্য এবং যিনি কার্যকারণ ঘটাতে সক্ষম। কার্যকারণ বলতে বুঝাচ্ছি, কোন ঘটনার পূর্ববর্তী অবস্থা বা পূর্ববর্তী সত্তা এবং পরবর্তী অবস্থা। কারণ (Cause) অবশ্যই তার ইফেক্ট বা ঘটনা ঘটানোর জন্য পর্যাপ্ত হতে হবে। যেমন, আতিকের হাত থেকে পরে গ্লাসটি ভেঙ্গে গিয়েছে। এখন গ্লাসটি ভাঙার পূর্ববর্তী ঘটনা হলো আতিকের হাত থেকে পরে যাওয়া এবং পরবর্তী ঘটনা হলো গ্লাসটি ভেঙ্গে যাওয়া।
যুক্তিটি ভালভাবে বুঝতে হলে কিছু ফিলোসফিক্যাল বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে। যেমন, সম্ভাব্য অস্তিত্ব, অসম্ভাব্য অস্তিত্ব, নির্ভরশীল অস্তিত্ব, অনিবার্য অস্তিত্ব, অনিবার্য বৈশিষ্ট্য (Essential Properties), আকস্মিক বৈশিষ্ট্য (Accidental Properties), PSR ইত্যাদি।
অনিবার্য অস্তিত্ব (Necessary Existence)
অনিবার্য অস্তিত্ব (Necessary Existence) বলতে বুঝায় কারণহীন কারণ, স্বাধীন অস্তিত্ব। মোডাল লজিক অনুসারে যে-সকল জিনিস বা অস্তিত্ব সকল সম্ভাব্য জগতে বাধ্যতামূলকভাবে অস্তিত্বশীল বা সত্য তাকে অপরিহার্য অস্তিত্ব বলে। যেমন ধরুন, একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহু থাকবে এটা অনিবার্য। প্রত্যেক সম্ভাব্য জগতে অনিবার্যভাবে ত্রিভুজের তিনটা বাহু থাকা লাগবে। এমন কোনো সম্ভাব্য জগতে নেই যেখানে ত্রিভুজের বাহু ৫টা বা ১০টা। এই ধরনের অস্তিত্বগুলো নেসেসারি। অনিবার্য অস্তিত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, অনিবার্য অস্তিত্ব তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন, ত্রিভুজের তিনটা বাহু। ত্রিভুজের তিনটা বাহু কিন্তু অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে হয়নি। বরং, নিজেই নিজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারে। মুসলিম দার্শনিক ইবনে সিনা নেসেসারি এক্সিস্টেন্সকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, “আমরা বলি যে প্রয়োজনীয় অস্তিত্ব (নেসেসারি এক্সিস্টেন্স) হলো অকারণ (অসৃষ্ট), যেখানে একটি ‘সামগ্রিক অস্তিত্ব’ (Contingent Existence) সৃষ্ট হয় এবং প্রয়োজনীয় অস্তিত্বটি (Necessary Existence) সমস্ত সম্ভাব্য উপায় এবং দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রয়োজনীয় (Necessary). [1]Mohammed Hijab; THE BURHĀN; Arguments for a Necessary Being Inspired by Islamic Thought; Page: 7
অপরিহার্য অস্তিত্বের প্রশ্নটি কসমোলজি, অন্টোলজি এবং ধর্মতত্ত্ব সহ অনুসন্ধানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। কসমোলজি দিয়ে শুরু করি। অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানী এবং মহাজাগতিক বিজ্ঞানীরা জগতের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। স্টিফেন হকিং বলেছেন যে একজন পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে তার লক্ষ্য হল “মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা, এটি যেভাবে আছে সেভাবে কেন আছে, এবং কেন অস্তিত্বশীল”। কসমোলজিস্ট শনক্যারল লিখেছেন, “আমরা বাস্তবতার একটি সম্পূর্ণ, সুসংগত এবং সহজ বোঝার সন্ধান করছি”। ব্রায়ান গ্রিন, একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, জোর দিয়ে বলেছেন যে “মহাবিশ্বের একটি চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়ার জন্য সবচেয়ে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করবে”।[2]Alexander R. Pruss and Joshua L. Rasmussen; Necessary Existence; Page: 4
বিজ্ঞানীদের এমন চূড়ান্ত ব্যাখ্যার অনুসন্ধান আমাদের মনে কিছু প্রশ্নের জানান দেয়, ঠিক কোন ধরনের ব্যাখ্যা আসলে চূড়ান্ত হতে পারে? নির্ভরশীল অস্তিত্ব কি চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হতে পারে? নাকি একটি অপরিহার্য বাস্তবতা বা অপরিহার্য অস্তিত্বের মধ্যেই আমাদের মহাবিশ্বের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নিহিত?
নাস্তিক পদার্থবিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস এর মতে, চূড়ান্ত নির্ভরশীল বাস্তবতার চূড়ান্ত ভিত্তি হলো ‘নাথিং’। তার ‘নাথিং’ শব্দটির মধ্যে ‘পদার্থ বিজ্ঞানের আইন এবং শর্ত অন্তর্ভুক্ত’। সুতরাং, লরেন্স ক্রাইস এর ‘নাথিং’ প্রকৃত অর্থে ‘নাথিং’ নয়। তাই সচেতন মানুষ মাত্রই জানতে চাইবে ‘পদার্থ বিজ্ঞানের আইন এবং শর্ত’ এগুলোর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা কি? কেন এই আইন বা শর্তগুলো অস্তিত্বশীল? এই আইনগুলোর পরিবর্তে কি অন্যান্য আইন থাকতে পারতো না? অবশ্যই পারতো। তাহলে ক্রাউস এর ‘নাথিং বা শূন্য’ আসলে জগতের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে না।
অনিবার্য অস্তিত্ব অন্টোলজির সাথেও প্রাসঙ্গিক। অন্টোলজিস্টরা বাস্তবতার মৌলিক বিষয়গুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করেন। বাস্তবতাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত, কনক্রিট (পদার্থ, ঘটনা), বিমূর্ত (সংখ্যা, সম্পর্ক, ইত্যাদি), মানসিক (অভিজ্ঞতা, চেতনা, অনুভূতি, ইত্যাদি)। অধিকাংশ দার্শনিকদের মতে কনক্রিট, বিমূর্ত, মানসিক বাস্তবতার মধ্যে যে পার্থক্য তা নির্ভরশীল ও অপরিহার্য অস্তিত্বের পার্থক্যের সাথে মিলে যায়। যাইহোক, কনক্রিট বাস্তবতা কি অপরিহার্য অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? যদি রিয়ালিটিতে বা বাস্তবে কোন কনক্রিট বাস্তবতা অপরিহার্যভাবে অস্তিত্বশীল হয় তবে কনক্রিট বাস্তবতা অপরিহার্য অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন কনক্রিট বাস্তবতা কি অপরিহার্যভাবে অস্তিত্বশীল? কিন্তু আমাদের কনক্রিট বাস্তবতার কোন কিছুই অপরিহার্যভাবে অস্তিত্বশীল নয়। কারণ এগুলো মূলত নির্ভরশীল এবং এগুলোর বিকল্প অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। এই বিষয়ে নিম্নে আরো বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।
ধর্মতত্ত্বে অনিবার্য অস্তিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধর্মতত্ত্বে অনিবার্য অস্তিত্ব হিসেবে স্রষ্টাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রায় সকল ধর্মেই স্রষ্টাকে অনিবার্য অস্তিত্ব হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়েছে।
অনিবার্য বৈশিষ্ট্য (Essential Properties)
অনিবার্য বৈশিষ্ট্য (Essential Properties) বলতে বুঝানো হয়, যে-সকল বৈশিষ্ট্য সকল সম্ভাব্য বস্তুর সাথে বাধ্যতামূলকভাবে অস্তিত্বে থাকবে তার বৈশিষ্ট্য হিসেবে৷ যেমন, ত্রিভুজের আইডেন্টিটি বা বৈশিষ্ট্য হলো তিন বাহু। যে-কোনো সম্ভাব্য জগতে তিন বাহু ছাড়া ত্রিভুজ হবে না। তাই ত্রিভুজের তিন বাহু হলো ত্রিভুজের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। একজন ব্যাচেলর এর সংজ্ঞা কি? যিনি বিয়ে করেনি। তার মানে প্রত্যেক সম্ভাব্য জগতে একজন ব্যাচেলর হবে অবিবাহিত। এমন কোনো সম্ভাব্য জগত নেই যেখানে একজন ব্যাচেলর বিবাহিত হবেন। তাই অবিবাহিত হওয়াটা ব্যাচেলরের জন্য অনিবার্য বৈশিষ্ট্য।
আকস্মিক বৈশিষ্ট্য (Accidental Properties)
আকস্মিক বৈশিষ্ট্য (Accidental Properties) হলো অনিবার্য বৈশিষ্ট্য এর বিপরীত। অনিবার্য বৈশিষ্ট্য এর ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলকভাবে থাকা লাগতো। যেমন, ব্যাচেলর। ব্যাচেলর এর অনিবার্য বৈশিষ্ট্য হলো অবিবাহিত হওয়া। তাই বাধ্যতামূলকভাবেই একজন ব্যাচেলর অবিবাহিত হবে। কিন্তু আকস্মিক বৈশিষ্ট্য এর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি তার উলটো। আকস্মিক বৈশিষ্ট্য গুলো বাধ্যতামূলকভাবে অস্তিত্বে নাও থাকতে পারে। যেমন, মানুষ মরণশীল। এটা মানুষের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানুষের অবস্থান বা কাজ এগুলো আকস্মিক বৈশিষ্ট্য। ধরুন, মাজেদ আল নোয়াব হলেন একজন ইসলামিক স্কলার। এটা তার আকস্মিক বৈশিষ্ট্য। মাজেদ আল নোয়াব বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামিক স্কলার হতেই হবে এমন না। তিনি দার্শনিক বা বিজ্ঞানীও হতে পারতেন। অন্যদিকে, মাজেদ আল নোয়াব হলো মরণশীল। এটা তার অনিবার্য বৈশিষ্ট্য।
সম্ভাব্য অস্তিত্ব এবং অসম্ভাব্য অস্তিত্ব
সম্ভাব্য অস্তিত্ব (Possible Existence) হলো একটা হাইপোথেটিক্যাল সিনারিও বা কোনো অস্তিত্বের অল্টারনেটিভ সিনারিও। অর্থাৎ, কোনো কিছু যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে না থেকে অন্যভাবেও থাকতে পারতো। যেমন, আপনি যে মোবাইলটি ফোনটি ব্যবহার করছেন, সেটার রং কালো। মোবাইলটি কালো না হয়ে সাদা বা নীল অথবা অন্য যে কোনো রং এর হতে পারতো। এটাই হচ্ছে সম্ভাব্য অস্তিত্ব। মোবাইলটি কালো রং এর না হয়ে অন্য যত রং এর হতে পারতো সেগুলো সব মোবাইলটির বর্তমান অবস্থার অল্টারনেটিভ সিনারিও। এক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ সিনারিও অবশ্যই ল অব লজিকের সূত্র অনুসরণ করতেই হবে। অর্থাৎ, কোনো একটা অস্তিত্বের যে সম্ভাব্য অপশনগুলো আছে বা অল্টারনেটিভ যে অপশনগুলো থাকতে পারতো সেগুলো যৌক্তিকভাবে সাংঘর্ষিক (Logical Contradiction) হতে পারবে না। যেমন, আমি যে মোবাইলটি ব্যবহার করছি সেটির রং কালো। মোবাইলটি কালো ব্যতীত অন্য রং এর হতে পারতো। কিন্তু যদি বলা হয় মোবাইলটি একই সাথে কালো এবং সাদা বা একই সাথে কালো এবং অন্য যে কোনো রং এর তাহলে তা যৌক্তিকভাবে সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে। অথবা এভাবেও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে, কোনো একজন লোক বিবাহিত। কিন্তু একই সাথে সে বিবাহিত আবার অবিবাহিত হতে পারবে না, কারণ তা যৌক্তিকভাবে সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে। সুতরাং, ফিলোসফির মোডাল লজিক এর ভিত্তিতে যেই জিনিসগুলো যৌক্তিকভাবে সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে না, সেগুলো সকল জিনিসের অস্তিত্ব সম্ভব বা সম্ভাব্য অস্তিত্ব। আর যেই জিনিসগুলো যৌক্তিক সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে সেগুলোর অসম্ভব বা অসম্ভাব্য অস্তিত্ব। কোনো কিছু যৌক্তিক সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে কিনা এটা বুঝতে হলে Laws of logic সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে। ‘যুক্তিবিদ্যা’[3]যুক্তিবিদ্যা কি ? – Faith and Theology (faith-and-theology.com) লিখাতে ল অব লজিকের নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।
সম্ভাবনার ধরন
সম্ভাবতা (possibility) মূলত দুই ধরণের। ১. যৌক্তিক সম্ভাব্যতা (logically possible). ২. বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতা (scientifically possible).
যৌক্তিকভাবে সম্ভব্যতা
যৌক্তিক সম্ভাব্যতা বলতে বুঝানো হয় ল অফ লজিকের সূত্র মোতাবেক যা কিছু হওয়া পসিবল তা। একজন অবিবাহিত মানুষের বউ থাকবেনা, একজন মানুষের একাধিক টি-শার্ট থাকতে পারে, এই দাবিগুলো প্রত্যেক সম্ভাব্য জগতে (Possible world) সত্য। কারণ এখানো কোনো যৌক্তিক সাংঘর্ষিকতা নেই। কিন্তু যদি বলা হয় যে, একজন অবিবাহিত মানুষের বউ আছে, বা একটা বর্গাকার বৃত্ত (square circle) তৈরি করা সম্ভব, একটি ত্রিভূজের ৫টি বাহু বা কোন থাকা সম্ভব তাহলে তা প্রত্যেক সম্ভাব্য জগতে মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে। কারণ, এই দবিগুলো যুক্তি বিদ্যার মৌলিক নীতির (laws of logic) বিরুদ্ধে অবস্থান করে। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার এর মূল কথা হলো, যা কিছু যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়মগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান করে না তা সম্ভাব্য বলে বিবেচিত হবে।
বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতা
বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতা বলতে বোঝায়, আমাদের মহাজগতে কিছু নিয়ম ফিক্সড, সেই নিয়মগুলোকে ভায়োলেট করা পসিবল না। যেমন, আমাদের কনক্রিট ওয়ার্ল্ডে আলোর গতি কনস্ট্যান্ট। আপনি এই কনক্রিট ওয়ার্ল্ডে আলোর গতি কনস্ট্যান্ট এটাকে ব্রেক করতে পারবেন না। কারণ এটা বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব বলে বিষয়টা এমন না যে, এটা যৌক্তিকভাবেও সম্ভব না। অর্থাৎ, এমন কোনো সম্ভাব্য জগৎ থাকতেই পারে যেখানে আমাদের প্রকৃতিতে পদার্থের নিয়মগুলো যেভাবে আছে তার ঠিক উলটোভাবে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কোনো প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ছাড়া কি আমরা আকাশে উড়তে পারবো কিনা? এর উত্তর হবে অবশ্যই না। কারণ, বৈজ্ঞানিকভাবে এটা সম্ভব না যে আমরা কোনো ধরনের প্রযুক্তি ছাড়া আকাশে উড়তে পারবো। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব না বলে এমন না যে এটা যৌক্তিকভাবেও সম্ভব না। এমন কোনো সম্ভাব্য জগত থাকতেই পারে যেখানে আমরা কোনো প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ছাড়াই আকাশে উড়তে পারবো।
পর্যাপ্ত কারণের নীতি (Principle of sufficient reason / PSR)
PSR অনুযায়ী সব কিছুর অস্তিত্বের জন্য পর্যাপ্ত কারণ ব্যাখ্যা রয়েছে। সবকিছুর পিছনে কারণ থাকাটা স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য। এটি ‘Principle of sufficient reason’ এর সংস্করণ। দার্শনিক লাইবনিজ তার কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে PSR ব্যাবহার করেছিলো। এটি সজ্ঞাতভাবে সুস্পষ্ট যে অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুরু আছে তার কারণ আছে। আমরা আমাদের চারপাশে যেসব জিনিস দেখি যেমন, চেয়ার, টেবিল, গাছপালা, ঘরবাড়ি ইত্যাদি। এগুলো কোনো কিছুই চিরকাল অস্তিত্বে ছিলোনা। বরং, একটা সময়ে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে এবং কোনো কারণ ছাড়াই এগুলো এমনি এমনি অস্তিত্বে চলে এসেছে এমন দাবিও যৌক্তিক নয়। তাহলে অবশ্যই অস্তিত্বে আসার জন্য কোনো-না-কোন কারণ প্রয়োজন। তাই কেউ চাইলেই এই ব্যখ্যার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। কারণ এটি স্বতঃসিদ্ধ।
PSR ইন্ডাক্টিভ মেথড দিয়েও প্রমাণ করা যায়। মানব জাতির ইতিহাসে আমরা অসংখ্য জিনিসের সম্মুখীন হয়েছি। তবে আমরা কখনোই এমন কোন জিনিসের সম্মুখীন হয়নি যা কোনও কারণ ছাড়াই এমনি এমনি অস্তিত্বে এসেছে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা ইন্ডাক্টিভ মেথডের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুরু আছে তার শুরুর কারণ আছে। ধরুন, আপনি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার ডিপার্টমেন্টের ক্লাসরুম গুলো কে তৌরি করেছে? জবাবে আপনার বন্ধু বললো, এগুলো কেউ তৌরি করেনি, এমনি এমনি অস্তিত্বে চলে এসেছে। এমন উত্তর শুনে নিশ্চয় তাকে হেমায়েতপুর পাঠানোর ব্যাবস্থা করবেন। কারণ এটা সম্ভব নয় যে কোনো কিছু এমনি এমনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে চলে এসেছে। বরং অস্তিত্বের জন্য সবকিছুর একটা কারণ (Cause) থাকা অনিবার্য। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, কোনো কিছু এমনি এমনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসতে পারেনা।
কিছু নাস্তিক এখানে দাবি করতে পারে যে, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনে ভার্চুয়াল পার্টিকেল কোনো কারণ ছাড়াই অস্তিত্বে চলে আসতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তারা দেখায় যে, Radio Active Decay বা তেজস্ক্রিয় ক্ষয় এর বিষয়টি। এই দাবিটা আসলে সত্য নয়। মূলত আইসোটোপ কার্বন -১৪ থেকে -১২ পর্যন্ত একক পরমাণুর তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সময় কীভাবে কি হবে তা আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। তেজস্ক্রিয় ক্ষয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা সহজাতভাবে সম্ভাব্য। সুতরাং, কোনো নির্দিষ্ট পরমাণু কখন ক্ষয় হবে তা বের করা অসম্ভব। কারণ তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সম্পূর্ণ র্যান্ডম অবস্থা। এক্ষেত্রে কার্যকারণ অজানা থাকে।[4]Protection and Dosimetry an Introduction to Health Physics. https://doi.org/10.1007/978-0-387-49983-3
তাত্ত্বিক কোয়ান্টাম পদার্থবিদ ক্যাসলাভ ব্রুকনার কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডে কার্যকারণকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, ধরুন আপনার সামনে একসারি ডমিনো সাজানো আছে। আপনি যখনই প্রথম ডমিনোটি ফেলে দিবেন তখন আস্তে আস্তে বাকি ডমিনো গুলো পরতে থাকবে একের পর এক। অর্থাৎ, A থেকে B ডমিনো, B থেকে C ডমিনো C থেকে D এভাবে পরতে থাকবে। এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকারণের উদাহরণ। তবে কোয়ান্টাম জগতে A ডমিনোর পতনের ফলে B ডমিনো পরবে নাকি C ডমিনো পরবে তা নির্ধারণ করা যায় না। ডমিনোর পতন A থেকে শুরু হবে নাকি B থেকে শুরু হবে তা অজানা থাকে। তাই কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডে কার্যকারণ অনির্ধারিত থাকে বা অজানা থাকে।[5]Caslav Brukner Causality in a quantum world. DOI.org/10.1063/PT.6.1.20180328a
রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে বলেছে কার্যকারণ তত্ত্ব সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং তা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। প্রফেসর ডি আরিয়ানো ২০১৮ সালে রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত এক পেপার ‘Causality re-established’ গবেষণায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে কার্যকারণ তত্ত্ব নিয়ে বলেন, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে কার্যকারণ কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি উপপাদ্য এবং এটি ফলসিফায়েবল এবং প্রেডিকশন তৈরি করতে সক্ষম। যার ফলে কার্ল পপারের ডিমার্কেশন ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী কার্যকারণ সবক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।[6]D’Ariano, G. M. (2018). Causality re-established. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 376(2123), 20170313
নির্ভরশীল অস্তিত্ব (contingent existence)
নির্ভরশীল অস্তিত্ব (Contingent Existence) হচ্ছে এমন কিছু যা অস্তিত্বে নাও থাকতে পারতো, অথবা যেভাবে আছে সেভাবে না থেকে অন্যভাবেও থাকতে পারতো। আমি জন্ম নাও নিতে পারতাম। তাই আমি কন্টিনজেন্ট। মোডাল লজিকে সেসকল জিনিসকে নির্ভরশীল অস্তিত্ব বলা হয় যা কিছু তার অস্তিত্বের জন্য কোনো না কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল বা যা কিছু বাধ্যতামূলকভাবে অস্তিত্বশীল হতেই হবে এমন নয়। আমাদের এই মহাবিশ্বের যা কিছু আমরা পর্যবেক্ষণ করি, অনুভব করি, তা সবকিছুই নির্ভরশীল। এগুলোর অস্তিত্ব বাধ্যতামূলক না। আমি, আপনি, আমাদের চারপাশের এই প্রকৃতি, এগুলো অস্তিত্বে নাও থাকতো পারতো। আপনি এখন যে চেয়ারে বসে বইটি পড়ছেন এটাও নির্ভরশীল। কারণ এরকম হাজারো অবস্থা আমরা কল্পনা করতে পারি যে এই চেয়ারটি তো প্রস্তুতকারি প্রস্তুত নাও পারতো, অথবা আপনি এটা নাও কিনতে পারতেন। আবার যেভাবে আছে সেভাবে না থেকে অন্যভাবেও থাকতে পারতো। যে সকল জিনিস এমন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তার অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা বা কারণ (Cause) প্রয়োজন। আপনি জিজ্ঞেস করতেই পারেন যে এটা তো নাও থাকতে পারতো, তাহলে কেন আছে? এটা কি নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে? নাকি কেউ এটাকে সৃষ্টি করেছে? এটার সেইপ এমন কেন হলো? কেউ এটাকে এই সেইপ দিয়েছে নাকি এটা নিজেই নিজের সেইপ এভাবে নির্ধারণ করেছে?
যা কিছু তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল তার অস্তিত্ব অনিবার্য বা নেসেসারি নয়। এবং তা অপ্রয়োজনীয়। যেমন ধরুন আপনি নিজেই নিজের অস্তিত্বের জন্য আপনার বাবা-মা, অক্সিজেন, খাবার, এমন অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যা কিছু তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল বা অপ্রয়োজনীয় তা নির্ভরশীল অস্তিত্ব (Contingent Existence). অপ্রয়োজনীয় বলতে বুঝানো হচ্ছে যেটা অস্তিত্বে থাকাটা জরুরি না বা অস্তিত্বে থাকতেই হবে বিষয়টা এমন না। সাধারণত আমরা প্রয়োজনীয় বলতে আমরা বুঝি যা আমাদের দরকার। কিন্তু দর্শনে যখন কোনো কিছুর অস্তিত্বকে প্রয়োজনীয় বলা হয় তখন তা অনিবার্য অস্তিত্ব। অর্থাৎ, যার অস্তিত্ব থাকতেই হবে। যার অস্তিত্ব না থাকাটা অসম্ভব বা যার অস্তিত্ব নেই এমনটা ভাবাও যায়না।
নির্ভরশীল অস্তিত্বের কারণ কি?
PSR অনুযায়ী যেহেতু সব কিছু অস্তিত্বশীল হওয়ার জন্য কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন তাই নির্ভরশীল অস্তিত্বগুলোর অস্তিত্বের জন্যও কারণ বা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এদের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা কি হতে পারে?
শূন্য থেকে সৃষ্ট?
শূন্য বলতে বুঝানো হয় যাবতীয় সবকিছুর অনুপস্থিতি। অর্থাৎ, সকল পদার্থ, শক্তি, সময় যাবতীয় সবকিছুর অনুপস্থিতি। অথবা শূন্য মানে কোনো কারণজনিত পরিবেশের অনুপস্থিতিকেও বোঝায়। এরকম একটা অবস্থা থেকে কোনো কিছুই সৃষ্টি হতে পারেনা। কেননা অস্তিত্বহীন কিছু থেকে কীভাবে একটা কিছু অস্তিত্বে আসতে পারে!? শূন্য থেকে কিছুই আসেনা। ০+০+০+=০ই হবে! কখনো ৩ হবেনা। ধরুন,
* গতকাল রাতে আপনার বন্ধুর বিয়েতে খুব মজা করে বিরিয়ানি খেলেন। কিন্তু সেটা কিছুই ছিল না!
* সেদিন পরীক্ষার হলে আমার পাশে কেউ বসেনি। কিন্তু তারা আমাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেখিয়েছিল
* আপনাকে কোনো এক নির্জন জায়গায় অন্ধকার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। দরজা-জানালা সব বন্ধ। আর নির্জন এলাকা বলে কেউ আপনার চিৎকারও শুনতে পাচ্ছেনা। আপনি বসে বসে ভাবছেন কীভাবে সেখান থেকে বের হবেন! কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে উঠেই দেখলেন সেই অন্ধকার নির্জন ঘরে একটা টেবিল রাখা, তার উপর একটা ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সংযোগ, বিদ্যুৎ সবই এমনি এমনি চলে আসছে।
উপরের তিনটি যুক্তি একজন সুস্থ বিবেকবান, যৌক্তিক মানুষ মাত্রই স্বীকার করবে এটা একেবারেই অসম্ভব এবং হাস্যকর। ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব?’ ব্যাপারটা ঠিক এরকমই অসম্ভব ও হাস্যকর! নাস্তিকরা দাবি করতে পারে কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম বা শূন্যতায় কোনো কণিকা শূন্য থেকে অস্তিত্বশীল হতে পারে। কিন্তু কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম বা শূন্যতা কোনো খালি জায়গা নয়। সেখানে পদার্থের নিয়ম চলে। কোয়ান্টাম শূন্যতা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী শক্তির অবস্থা। আর সেই শক্তি থেকেই প্রতিনিয়ত জোড়ায় জোড়ায় তৈরি হয় কণা ও প্রতিকণা। যারা পুনরায় ধ্বংস হয়ে আবার শক্তিতে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম বা শূন্যতা মানে ভৌত কিছু।[7] Physics – The Force of Empty Space (aps.org)
স্ব-সৃষ্ট?
নির্ভরশীল অস্তিত্বগুলো কি নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করতে পারবে? যেমন, আমি কি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে করতে পারবো? একটা আপেল কি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারবে? ইউনিভার্স কি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারবে?
সৃষ্টি বলতে বুঝানো হয় কোনো কিছু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসা। অর্থাৎ যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না পরবর্তীতে অস্তিত্বে এসেছে। তার মানে কোনো কিছু সৃষ্টি হলে সৃষ্টির পূর্বে তাকে অনস্তিত্বে থাকতে হবে। এখন কোনো বস্তু বা সত্তা যদি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে তাহলে সে অস্তিত্বে এসেছে অনস্তিত্ব থেকে। অস্তিত্বশীল হওয়ার পূর্বে সে ছিলো অস্তিত্বহীণ। আবার, Principle of sufficient reason (PSR) অনুযায়ী অস্তিত্বের জন্য সব কিছুর অবশ্যই কারণ থাকবে। তাহলে কোনো বস্তু বা সত্তার অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসার জন্যও কারণ থাকা লাগবে। তাই কোনো বস্তু বা সত্তা যদি নিজেই নিজের অস্তিত্বের কারণ হওয়ার মানে অস্তিত্বশীল হওয়ার জন্য অস্তিত্বে আসার পূর্বে অস্তিত্বের কারণ হিসেবে তাকে অস্তিত্বশীল হতে হচ্ছে। অর্থাৎ, কোনো কিছু যদি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে তাহলে একই সময় তাকে অস্তিত্বে থাকা লাগবে আবার অনস্তিত্বে থাকা লাগবে যা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব।
উদাহরণস্বরূপ, ‘ক’ নামক ব্যক্তি জন্ম নেওয়ার আগেই কি ‘ক’ নামক ব্যক্তি অস্তিত্বে থাকতে পারবে? বিষয়টা আরো একটু সহজভাবে ব্যাখ্যা করি। ধরুন, ‘ক’ নামক ব্যক্তি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে। এখন সৃষ্টি মানে যেহেতু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসা তার মানে ‘ক’ নামক ব্যক্তিও অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে। অর্থাৎ, অস্তিত্বে আসার পূর্বে ‘ক’ ছিল অস্তিত্বহীন। Principle of sufficient reason (PSR) নিয়ম অনুযায়ী ‘ক’ অস্তিত্বে আসতে হলে অবশ্যই একটা কারণ লাগবে। যেহেতু ‘ক’ নামক ব্যক্তি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে সেহেতু ‘ক’ নামক ব্যক্তির কারণ সে নিজেই। সুতরাং ‘ক’ নামক ব্যক্তি অস্তিত্বে আসার আগেই নিজের অস্তিত্বের কারণ হিসেবে অস্তিত্বে থাকতে হচ্ছে। সুতরাং, ‘ক’ নামক ব্যক্তি যদি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে তাহলে একই সময় তাকে অস্তিত্বে থাকা লাগবে আবার অনস্তিত্বে থাকা লাগবে। যা Low of Logic এর দ্বিতীয় সূত্র Low of Non-contradiction কে ভায়োলেট করে। যা Principle of noncontradiction (PNC) নামেও পরিচিত। Low of Non-contradiction বলতে বুঝানো হয় সাংঘর্ষিক কোনো কিছুই অস্তিত্বে থাকতে পারেনা। যেমন, N= True, N= False. এখানে N একই সাথে সত্য আবার মিথ্যা। কোনো জিনিস একই সময় পারস্পরিক দ্বন্দ্বমূলক অবস্থায় থাকা সম্ভব না।
Principle of noncontradiction কে অস্বীকার করা অসম্ভব। কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। একটা দৃশ্যপট কল্পনা করুন, সিফাত নামের এক লোক বললো যে সে Principle of noncontradiction কে বিশ্বাস করে না। যেহেতু সে Principle of noncontradiction বিশ্বাস করে না সেহেতু তার মতে কোনো জিনিস একই সাথে সত্য আবার মিথ্যা হতে পারে। অর্থাৎ, তার বিশ্বাস করা আর বিশ্বাস না করা দুটো একই সময়ে একই। সুতরাং, সিফাত যখনই বলেছে সে, Principle of noncontradiction বিশ্বাস করেনা ঠিক তখনই তার মতে সে Principle of noncontradiction বিশ্বাস করে। অর্থাৎ, Principle of noncontradiction কে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।
অন্য কোনো সৃষ্ট সত্তা থেকে সৃষ্ট?
পরনির্ভরশীল বস্তু বা সত্তা কি অন্য কোনো সৃষ্ট সত্তা থেকে সৃষ্ট? অথবা আমাদের এই মহাবিশ্ব যেহেতু পর-নির্ভরশীল এবং এর অস্তিত্ব যেহেতু শূন্য থেকে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়, আবার স্ব-সৃষ্টও নয় সেহেতু মহাবিশ্ব কি এমন কোনো সত্তা থেকে সৃষ্টি হতে পারে যে কিনা আবার অন্য কোনো সত্তা থেকে সৃষ্ট? তর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরেও নিই যে, হুম এই মহাবিশ্ব এমন কোনো সত্তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে যে সত্তা আবার অন্য কোনো সত্তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এমন উত্তর শুনে একজন যৌক্তিক মানুষ মাত্রই আপনাকে প্রশ্ন করবে তাহলে সেই সত্তাকে কে সৃষ্টি করেছে? যদি এই প্রশ্নের জবাবে এমন উত্তর আসে যে, সেই সত্তাকে অন্য কোনো সত্তা সৃষ্টি করেছে। তাহলে আবারো একই প্রশ্ন আসবে যে তাহলে সেই সত্তাকে কে সৃষ্টি করেছে? এভাবে প্রশ্ন আজীবন চলতে থাকবে যদি শুরুতে এমন একজন সত্তা না থাকে যে সত্তা হলেন অসৃষ্ট।
কার্যকারণ সম্বন্ধ কি অসীম হতে পারে?
যদি কোন সৃষ্ট বস্তু এমন কোনো সত্তা থেকে সৃষ্টি হয় যে সত্তা আবার অন্যকোনো সৃষ্ট সত্তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে তাহলে প্রশ্ন আসবে, সেই সৃষ্ট সত্তাকে কে সৃষ্টি করেছে? এভাবে প্রশ্ন করার এই প্রক্রিয়া আজীবন পিছনের দিকে যেতেই থাকবে। অর্থাৎ, কার্যকারণ সম্বন্ধ হবে অসীম। অসীম বলতে, সীমাহীন, অন্তহীন বা যে কোনো সংখ্যার চেয়ে বড় কিছুকে বুঝায়। নির্ভরশীল কোনো কিছুর অস্তিত্ব অসীম হতে পারেনা। কেননা প্রকৃত অসীম বাস্তবে অস্তিত্বশীল নয়। যদি কোনো সৃষ্ট বস্তুর কার্যকারণ অসীম হয় তাহলে সে বস্তু সৃষ্টি হবেনা বা বর্তমানে আসবেনা। তাও শুধুমাত্র আলোচনার খাতিরে যদি আমরা ধরেই নেই যে কোন সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের জন্য অসীম সংখ্যক কারণ রয়েছে। কিন্তু আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন অসীমের এই ব্যাখ্যায় আপনি প্রশ্নকারীকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না।
উদাহরণস্বরূপ, আমাদের মহাবিশ্ব সৃষ্ট এবং একে যদি আমরা ‘X’ ধরি তাহলে এবং ‘X’ এর অস্তিত্বের কারণ যদি হয় ‘X 1’, আবার ‘X1’ এর অস্তিত্বের কারণ যদি হয় ‘X2’ আর এভাবে যদি অনন্তকাল চলতে থাকে তাহলে ‘X’ কখনোই অস্তিত্বে আসতে পারবেনা! কেননা ‘X’ অস্তিত্বে আসার জন্য নির্ভর করে ‘X1’ এর উপর, আবার ‘X1’ অস্তিত্বে আসার জন্য নির্ভর করে ‘X2’ এর উপর এবং এভাবে যদি অনন্তকাল চলতে থাকে তাহলে ‘X’ অস্তিত্বে আসার জন্য নির্ভর করে অনাদিকাল ধরে চলা সৃষ্ট কিছুর উপর। এইভাবে অনাদিকাল ধরে চলা সৃষ্ট কিছুর উপর নির্ভর করলে ‘অনবস্থা দোষ’ (Infinite regress) দেখা দিবে। সুতরাং, মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসার জন্য অসীম সংখ্যক কারণ বা মহাবিশ্ব অসীম হওয়া সম্ভব না। বরং মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য শুরুতে এমন একটা কারণ থাকা অনিবার্য যেটা কারণহীন কারণ।
একটা থট এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে বুঝার চেষ্টা করি। ধরুন আপনি চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাওয়ার জন্য টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে বাসে উঠতে গেলেন। বাসের সামনে গিয়ে দেখলেন আপনার সামনে কিছু সংখ্যক যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে কি আপনি বাসে উঠতে পারবেন? অবশ্যই পারবেন। কারণ আপনার সামনে কিছু সংখ্যক যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকা কিছু সংখ্যক যাত্রী বাসে উঠার পরেই আপনি বাসে উঠতে পারবেন।
এখন দৃশ্যপটটি ঠিক উলটোভাবে চিন্তা করুন। টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে আপনি বাসে উঠতে গিয়ে দেখলেন যে আপনার সামনে অসীম সংখ্যক যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে কি আপনি কখনোই বাসে উঠতে পারবেন? অবশ্যই পারবেন না। কারণ আপনার সামনে যেহেতু অসীম সংখ্যক যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে, এই অসীম সংখ্যক যাত্রীর বাসে উঠার পরেই আপনি বাসে উঠতে পারবেন। কিন্তু অসীম সংখ্যক যাত্রীর বাসে উঠতে সময়ও লাগবে অসীম। আর অসীম যেহেতু কখনো শেষ হবে না তাই আপনার বাসে উঠাও কখনো হবে না। এখন এই উদাহরণটি মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে চিন্তা করুন। আপনার বাসে উঠা = মহাবিশ্ব। আর আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অসীম সংখ্যক যাত্রী = মহাবিশ্বের পেছনের অসীম সংখ্যক কারণ। যদি এমন হয় তাহলে কি কখনোই এই মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসতে পারবে? অবশ্যই না! কোনো কিছু অস্তিত্বের জন্য যদি অতীতে অসীম সংখ্যক কারণের উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে তা ইনফিনিটি রিগ্রেস এর কারণে কখনোই বর্তমানে আসতে পারবে না। মুসলিম দার্শনিক ইবনে সিনা বলেন, “সামগ্রিক অস্তিত্বের (নির্ভরশীল অস্তিত্ব) সেটটি (set) ব্যাখ্যা করার জন্য সেটের বাইরে একটি অনিবার্য অস্তিত্বের প্রয়োজন”। ‘অসীম’ সম্পর্কে আরো বিষদ আলোচনা থাকবে কালাম কসমোলজি আর্গুমেন্টে।
অসৃষ্ট থেকে সৃষ্ট
যেহেতু নির্ভরশীল অস্তিত্ব নিজে থেকে সৃষ্টি হতে পারেনা, শূন্য থেকেও সৃষ্টি হতে পারেনা এবং এর কারণ অসীমও হতে পারেনা তাহলে এর বিকল্প কী? বিকল্প হচ্ছে এটি এমন একটি সত্তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে যা কারণহীন কারণ (অস্তিত্বের জন্য কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নয়) বা অনাদী (eternal) সত্তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ, যা সব সময়ই অস্তিত্বশীল (চিরন্তন)। পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাসে এই সত্যতা জ্বল জ্বল করছে। পবিত্র কুরআনে সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে, “বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই”।[8]সূরা ইখলাস; ১১২: ১-৪
মূল যুক্তি
শুরুতেই বলেছি, এই যুক্তিটির মূল উপাদান হল একটি কার্যকারণ নীতি। যেমন, যা কিছু অস্তিত্বে ব্যর্থ হতে পারতো বা বিকল্প অস্তিত্ব হতে পারতো তার অস্তিত্বের জন্য একটি কারণ রয়েছে। এই যুক্তিতে এটাই দেখানো হয় যে আমাদের এই মহাবিশ্বের যা কিছু আমরা পর্যবেক্ষণ করি বা অনুভব করি তার সব কিছুই পর-নির্ভরশীল। এগুলো অস্তিত্বের জন্য ব্যর্থ হতে পারতো। এ কারণেই এসব অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা বা কারণ প্রয়োজন। এর একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, পর-নির্ভরশীল অস্তিত্ব এমন এক সত্তার উপর নির্ভরশীল যার অস্তিত্ব এই মহাজগৎ থেকে স্বাধীন, যে সত্তা তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভশীল নয়, যে সত্তা হবে চিরন্তন এবং অনিবার্য অস্তিত্বশীল (যার অস্তিত্ব না থাকা অসম্ভব)। অন্যথায় পর-নির্ভরশীল এর কারণগুলোর সাথে আরো একটি পর-নির্ভরশীল কারণ যুক্ত হবে এবং কারণের এই ধারাবাহিকতা অসীমকাল ধরেই চলতে থাকবে। যার ফলে ইনফিনিটি রিগ্রেস ঘটবে। এই মহাবিশ্বের যা কিছু আমরা পর্যবেক্ষণ, অনুভব করি তা যে পর-নির্ভরশীল তা যেভাবে বুঝতে পারি,
১. পরনির্ভরশীল জিনিসের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা অপ্রয়োজনীয়। অপ্রয়োজনীয় বলতে বুঝায়, এগুলোর অস্তিত্ব থাকতেই হবে বা এগুলো অনিবার্য নয়। থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। একটা দৃশ্যপট কল্পনা করুন, কোন এক শীতের স্নিগ্ধ সকালে মেঠো পথের প্রান্তরে হেঁটে চলেছেন আপনার বন্ধুর সাথে। হঠাৎ, রাস্তার পাশে একটা ফুটবল লক্ষ করলেন। ফুটবলটি দেখে নিশ্চয়ই আপনি এমনটা কল্পনা করবেন না যে, এটা এমনি এমনি এখানে চলে এসেছে। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগবে ফুটবলটা এখানে কেন এসেছে? এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটা হতে পারে, কেউ হয়ত ভুল করে এখানে ফেলে দিয়েছে। কারণ ফুটবলটি এখানে থাকার কথা নয়। এটা এখানে থাকাটা প্রয়োজনীয় নয়। এই ফুটবলটি যে এখানে রেখে দিয়েছে সে এখানে নাও রাখতে পারতো। ফুটবল প্রস্তুতকারী কোম্পানি এটাকে নাও তৈরি করতে পারতো। যে এখানে রেখে গেছে সে এটা নাও কিনতে পারতো। সুতরাং, ফুটবলটি এখানে থাকার জন্য একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হচ্ছে। তার মানে এটা পরনির্ভরশীল। একইভাবে আমাদের এই মহাবিশ্ব যেভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে তা নাও হতে পারতো। মহাবিশ্ব অস্তিত্বে নাও থাকতে পারতো, এর নিয়মগুলো যেমন আছে ঠিক তেমন নাও হতে পারতো। কারণ এই সম্ভাবনাগুলো যৌক্তিকভাবে কোনো প্রকার সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে না, বা এগুলো যৌক্তিকভাবে অসম্ভব এমন কিছু না।
কেউ হয়ত দাবি করতে পারে যে মহাবিশ্বের নিয়মগুলো যেভাবে আছে তার বিপরীতভাবে থাকতে পারে না। কারণ, অন্যভাবে থাকলে মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু এই দাবিই এটা প্রমাণ করে না যে, নিয়মগুলো অন্যভাবে থাকাটা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব। বরং, এই দাবি প্রমাণ করে নিয়মগুলো যেভাবে আছে সেভাবে না থাকাটা বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব। আমরা সম্ভাব্য অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনাতে জেনেছি যে, যা কিছু যৌক্তিকভাবে সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে না তা সবকিছুরই অস্তিত্বে থাকা সম্ভব। সুতরাং, মহাবিশ্ব যেভাবে আছে সেভাবে নাও থাকতে পারতো, বা এর অস্তিত্বই না থাকতে পারতো, এটা যৌক্তিকভাবে সম্ভব।
২. কোনো জিনিসের উপাদানগুলোকে যদি যেভাবে আছে তার বিপরীতেও ব্যাখ্যা করা যায় সেক্ষেত্রেও সেটা পর-নির্ভর। নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুণ,
মৃদু আলো আর সোডিয়াম বাতির ঝলসানো রাতের কোনো এক শূন্য রাস্তায় আপনি আর আপনার বন্ধু হেঁটে চলেছেন দিকভ্রান্ত পথিকের মতো। হঠাৎ একটা গোল চত্বরে আসতেই আপনার চোখে পড়লো ফুল দিয়ে সজ্জিত করা তিনটি শব্দ ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি’। আপনার ভেতরে প্রশ্ন জাগতে পারে, ফুল গুলো এভাবে সজ্জিত না করে অন্যভাবেও তো করা যেত! ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি’ এ কথার পরিবর্তে তো ‘আমি তোমাকে পছন্দ করি’ এভাবেও সজ্জিত করা যেত। কারণ এভাবে সজ্জিত হওয়ার যৌক্তিকভাবে অসম্ভব কিছু না। যেহেতু ফুলগুলো এভাবে সজ্জিত না থেকে অন্যভাবে সজ্জিত থাকতে পারতো, তাই কেন এভাবে আছে এটার একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ফুলগুলো গাছে থাকার কথা ছিলো, কেনই বা রাস্তায় এভাবে সজ্জিত অবস্থায় রয়েছে? কেউ যদি বলে ফুলগুলো এমনি এমনি এভাবে সজ্জিত হয়েছে আপনি নিশ্চয় তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটি হতে পারে এমন যে, কেউ একজন গাছ থেকে ফুলগুলো তুলে এনেছে, তারপর রাস্তার উপর এগুলোর বিন্যাস নির্ধারণ করেছে সজ্জিত করেছে। এটাই হচ্ছে ফুলগুলো ওভাবে সজ্জিত হওয়ার বাহ্যিক কারণ। সুতরাং, ফুলগুলো ওভাবে সজ্জিত থাকাটা হচ্ছে পর-নির্ভরশীল। একইভাবে আমাদের এই মহাবিশ্ব ঠিক যেভাবে সজ্জিত করা রয়েছে, এটা ঠিক তার উল্টোভাবেই থাকতে পারতো। এই ভেতরের পদার্থের নিয়মগুলো অন্যরকম হতে পারতো। কারণ অন্যভাবে থাকাটা যৌক্তিকভাবে কোনো প্রকার অসংগতি তৈরি করে না। যেমন, প্রাণের টিকে থাকার জন্য চাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো, পৃথিবীকে নিজ অক্ষের ওপর ২৩ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকতে সাহায্য করে। যদি এমনটা না হতো তাহলে পৃথিবীতে তাপমাত্রা এতোটাই সংকটময় হয়ে পরতো যে এখানে প্রাণের বিকাশ সম্ভব হতো না। কিন্তু এমন কোনো পসিবল ওয়ার্ল্ড থাকতে পারে যেখানে চাঁদ নিজেই অস্তিত্বে নেই, অথবা পৃথিবীরই অস্তিত্ব নেই। কারণ এগুলোর অস্তিত্বে না থাকাটা যৌক্তিকভাবে কোন রকম সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে না। সুতরাং, মহাবিশ্বের উপাদানগুলো ঠিক যেভাবে আছে তার বিপরীতভাবেও থাকা সম্ভব ছিলো। তাই মহাবিশ্ব পর-নির্ভরশীল অস্তিত্ব।
৩. পরনির্ভরশীল জিনিসের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এদের রূপগত গুণের সীমাবদ্ধতা। যেমন, কোনো কিছুর রং, আকার, ভর, তাপমাত্রা, আকৃতি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ইউনিভার্সের প্রত্যেকটি বস্তুর নির্দিষ্ট রং, আকার, আকৃতি আছে। কিন্তু এটা এভাবে না হয়ে অন্যভাবেও তো হতে পারতো। আমরা সেগুলোকে যেভাবে আছে তার বিপরীতভাবে চিন্তা করতে পারি। তার মানে এগুলো যেভাবে আছে সেটা কেউ নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা না হলে, কেন এই বস্তু গুলোর আকার যেভাবে আছে সেভাবে না থেকে অন্যভাবে হয়নি? কেন বস্তুগুলোর রং অন্য ধরনের হয়নি? বস্তুগুলোতে নিজেই নিজের সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করেনি। একটা ফুটবল হাতে নিয়ে নিশ্চয় আপনি এ কথা বলবেন না যে, ফুটবল নিজেই তার রং, আকার, ভর নির্ধারণ করেছে! সুতরাং এই রূপগত সীমাবদ্ধতাই প্রমাণ করে এগুলো পর-নির্ভরশীল অস্তিত্ব।
ধরুন, আপনি দোকান থেকে একটি কেক অর্ডার করলেন। কেক খাওয়ার পর আপনার ছোট ভাই বললো অনিবার্য কারণেই কেকের স্বাদ এমন, আকার এমন, রং এমন। এটা নিশ্চয় যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না। কারণ, কেকটির স্বাদ, আকার, রং, সম্পূর্ণ নির্ভর করে এর নির্মাতার হাতে। কেকটি নিজেই নিজের স্বাদ, আকার, রং নির্ধারণ করেনি। সুতরাং, যে-সব জিনিসের রুপগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা পরনির্ভরশীল। একইভাবে আমাদের এই মহাবিশ্বের আকার, তাপমাত্রা, রং, যেভাবে আছে সেভাবে না থেকে অন্যভাবেও থাকতো পারতো। গাছের পাতা সবুজ না হয়ে অন্য রং এর হতে পারতো। প্রকৃতির নিয়ম (law of nature) অন্যভাবেও হতে পারতো। মহাবিশ্ব নিজেই নিজের আকার ধারণ করেনি, নিজেই নিয়ম গুলো তৈরি করেনি। তার মানে এগুলো কেউ নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং, মহাবিশ্ব পর-নির্ভরশীল।
৪. পরনির্ভরশীলতার অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সসীমতা। আমাদের এই মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরে যা কিছু আমরা পর্যবেক্ষণ করি, যা কিছু আমরা অনুভব করি তার সব কিছুই সসীম। বিগ ব্যাং মডেল থেকে আমরা জানতে পারি আমাদের এই মহাবিশ্বের একটা শুরু আছে। এই বিষয়ে ‘মহাবিস্ফোরণ এবং অতঃপর মহাবিশ্ব’ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
পরনির্ভরশীলতার এসব বৈশিষ্ট্য গুলো বুঝতে পারলে আমরা এটা বুঝতে পারি যে আমাদের এই মহাজগৎ এবং তার মধ্যে যা কিছুর আমরা অনুভব করি, পর্যবেক্ষণ করি তার সবকিছুই পরনির্ভরশীল। সুতরাং, এই মহাবিশ্বের যা কিছু আমরা পর্যবেক্ষণ করি, অনুভব করি তা পরনির্ভরশীল।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা একটা ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্টের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি। যুক্তির বিবৃতি নিম্নরূপ;
- P1: Everything that exists has an explanation of its existence. (যা কিছু অস্তিত্বশীল তার অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন)
- P2: The universe exists. (মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল)
- P3: Therefore, the universe has an explanation for its existence. (এতএব, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য একটি ব্যাখ্যা আছে)
- P4: That explanation is either explained by its own nature or some external thing. (সেই ব্যাখ্যাটি হয় তার নিজস্ব প্রকৃতির দ্বারা অথবা কোন বাহ্যিক জিনিস দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।)
- P5: The explanation is a necessary Being/ God. (সেই ব্যাখ্যাটি হচ্ছে অনিবার্য অস্তিত্ব বা স্রষ্টা।)
- Conclusion: Therefore, God exists. (সুতরাং, স্রষ্টা অস্তিত্বশীল)
ব্যাখ্যা;
- P1: Everything that exists has an explanation of its existence. (যা কিছু অস্তিত্বশীল তার অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন)
PSR নিয়ে আলোচনাতে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি যে যা কিছু অস্তিত্বশীল তার অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং এটি স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য। P1 হচ্ছে ‘Principle of sufficient reason’ এর সংস্করণ। এটি দার্শনিক লাইবনিজ তার কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যাবহার করেছিলো। এটি সজ্ঞাতভাবে সুস্পষ্ট যে অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুরু আছে তার কারণ আছে। আমরা আমাদের চারপাশে যেসব জিনিস দেখি যেমন, চেয়ার, টেবিল, গাছপালা, ঘরবাড়ি ইত্যাদি। এগুলো কোনো কিছুই চিরকাল অস্তিত্বে ছিলোনা। বরং, একটা সময়ে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে। এবং কোনো কারণ ছাড়াই এগুলো এমনি এমনি অস্তিত্বে চলে এসেছে এমন দাবিও যৌক্তিক নয়। তাহলে অবশ্যই অস্তিত্বে আসার জন্য কোনো কারণ প্রয়োজন। তাই কেউ চাইলেই এই ব্যখ্যার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। কারণ এটি স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য। সুতরাং, P1 সত্য।
P1 ইন্ডাক্টিভ মেথড দিয়েও প্রমাণ করা যায়। মানব জাতির ইতিহাসে আমরা অসংখ্য জিনিসের সম্মুখীন হয়েছি। তবে আমরা কখনোই এমন কোন জিনিসের সম্মুখীন হয়নি যা কোনও কারণ ছাড়াই এমনি এমনি অস্তিত্বে এসেছে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা ইন্ডাক্টিভ মেথডে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, অস্তিত্বের জন্য যা কিছুর শুরু আছে তার শুরুর কারণ আছে। ধরুন, আপনি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার ডিপার্টমেন্টের ক্লাসরুম গুলো কে তৌরি করেছে? জবাবে আপনার বন্ধু বললো, এগুলো কেউ তৌরি করেনি, এমনি এমনি অস্তিত্বে চলে এসেছে। এমন উত্তর শুনে নিশ্চয় তাকে হেমায়েতপুর পাঠানোর ব্যাবস্থা করবেন। কারণ এটা সম্ভব নয় যে কোনো কিছু এমনি এমনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে চলে এসেছে। বরং অস্তিত্বে আসার জন্য সবকিছুর একটা কারণ (Cause) থাকা অনিবার্য। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, কোনো কিছু এমনি এমনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসতে পারেনা।
- P2: The universe exists. (মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল)
আমাদের মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য। তাই এটার সাথেও কেউ দ্বিমত করতে পারবে না। যদি কেউ দ্বিমত করে তাহলে তাকে প্রমাণ দিতে হবে যে কেন মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল না। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, প্রেমিস-২ (P2) সত্য।
- P3: Therefore, the universe has an explanation for its existence. (এতএব, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য একটি ব্যাখ্যা আছে)
P1 এবং P2 তে থেকে আমরা জেনেছি যে যা কিছু অস্তিত্বে আছে তার অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যেহেতু, আমাদের এই মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল সেহেতু মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য অবশ্যই ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সুতরাং, P1 এবং P2 এর মতো P3 সত্য হতে বাধ্য।
- P4: That explanation is either explained by its own nature or some external thing. (সেই ব্যাখ্যাটি হয় তার নিজস্ব প্রকৃতির দ্বারা অথবা কোন বাহ্যিক জিনিস দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।)
যেহেতু, আমাদের এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, এটার শুরু আছে, এটা নির্ভরশীল, তাই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাটি অবশ্যই বাহ্যিক কোনো কারণ হতে হবে। ‘মহা বিস্ফোরণ এবং অতঃপর মহাবিশ্ব’ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে আমাদের এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য শুরু আছে। মহাবিশ্ব অসীম সময় থেকে অস্তিত্বে ছিলো না। ‘নির্ভরশীল অস্তিত্ব’ অংশে আমরা দেখিয়েছি যে, যা কিছুর অস্তিত্ব যদি এমন হয় যে সেটা অস্তিত্বে থাকতেও পারতো আবার নাও থাকতে পারতো তাহলে তা নির্ভরশীল। আবার কোনো কিছু যদি যেভাবে আছে সেভাবে না থেকে অন্যভাবেও থাকা সম্ভব হয়, অর্থাৎ, যদি রি অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব হয় তাহলে সেটাও নির্ভরশীল। যেহেতু আমাদের এই মহাবিশ্ব বা মহাবিশ্বের ভেতরে যা কিছু আমরা পর্যবেক্ষণ করি, অনুভব করি তা অনিবার্য বা বাধ্যতামূলকভাবে অস্তিত্বশীল হতেই হবে এমন নয়, এগুলো কে আমরা যেভাবে আছে তার বিপরীতেও চিন্তা করতে পারি। মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে তা অনিবার্য (Essential Properties) নয় আকস্মিক (Accidental Properties)। তাই আমাদের মহাবিশ্ব পরনির্ভরশীল। এখানে যা কিছু অস্তিত্বশীল তা চিরন্তন, অনিবার্য এবং স্বাধীন নয়। পরনির্ভরশীল, সসীম, অস্তিত্বগুলো নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারেনা। যেহেতু আমাদের এই মহাবিশ্ব পরনির্ভরশীল, সসীম। তাই মহাবিশ্বও স্বসৃষ্ট হতে পারে না। ‘নির্ভরশীল অস্তিত্বগুলো কি স্বসৃষ্ট’ অংশেও ইতিমধ্যে স্ব-সৃষ্ট কেন সম্ভব না তা ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং, P4 সত্য।
- P5: The explanation is a necessary Being/ God. (সেই ব্যাখ্যাটি হচ্ছে অনিবার্য অনিবার্য অস্তিত্ব বা স্রষ্টা।)
PSR থেকে আমরা জানাতে পেরেছি অস্তিত্বের জন্য সব কিছুর কারণ বা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমরা অনিবার্য অস্তিত্ব এবং নির্ভরশীল অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেছি। নির্ভরশীল অস্তিত্বগুলো তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে এবং অস্তিত্বে আসার জন্য কার্যকারণ সম্পর্কও অসীম হতে পারে না। ইতিমধ্যে ‘কার্যকরণ সম্বন্ধ কি অসীম হতে পারে’ অংশে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেহেতু আমাদের এই মহাবিশ্ব পর-নির্ভরশীল এবং পর-নির্ভরশীল অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা বা কারণ প্রয়োজন, আর সেই ব্যাখ্যাটি অসীম সংখ্যক হতে পারবেনা, সেহেতু শুরুতে এমন একটা কারণ বা ব্যাখ্যা থাকা লাগবে যা কারণহীন কারণ, স্বাধীন, স্ব-নির্ভর, চিরন্তন, এবং অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল। যদি কারণ বা ব্যাখ্যাটি স্বাধীন, স্ব-নির্ভর, চিরন্তন, এবং অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল না হয় তাহলে ইনফিনিটি রিগ্রেসে পতিত হবে। ফলে মহাবিশ্ব সৃষ্টিই হতে পারতো না। সুতরাং, P5 সত্য।
- Conclusion: Therefore, God exists. (সুতরাং, স্রষ্টা অস্তিত্বশীল)
কারণহীন কারণ, স্বাধীন, স্ব-নির্ভর, চিরন্তন, এবং অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল বৈশিষ্ট্যগুলি একমাত্র স্রষ্টার প্রকৃতির সাথে খাপ খায়। এছাড়াও, ডিডাক্টিভ আর্গুমেন্ট অনুসারে যদি প্রেমিস (P) সত্য হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত (Conclusion) সত্য হতে বাধ্য। সুতরাং, ‘স্রষ্টা অস্তিত্বশীল’ এই সিদ্ধান্তটি সত্য হতে বাধ্য।
স্রষ্টার প্রকৃতি
স্রষ্টা হলো; এই প্রাকৃতিক জগতের বাহিরের এক অতিপ্রাকৃতিক সত্তা যিনি সর্বোচ্চ বা চূড়ান্ত বাস্তবতা, যিনি সর্বশক্তিমান, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান, নিখুঁত সত্তা, এবং তিনি উপাসনা যোগ্য। অধিকাংশ দার্শনিক বিশ্বাস করেন যে স্রষ্টার প্রকৃতি হল; সর্বশক্তিমানতা, সর্বজ্ঞতা, এবং একক হিসেবে। স্রষ্টার এই গুণগুলো স্রষ্টাকে অনন্য, সুনিপুণ, এবং উপাসনার যোগ্য করে তোলে। স্রষ্টার এই গুণগুলো তার অপরিহার্য গুণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সর্বজ্ঞ হওয়ার মানে তিনি সবকিছু জানেন, সর্বশক্তিমান হওয়ার মানে তিনি সবকিছু (যা কিছু যৌক্তিকভাবে সম্ভব) করতে পারেন, এবং একক হওয়ার মানে তার সমকক্ষ আর কেউ নেই বা তিনি অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়।
স্রষ্টা সর্বশক্তিমান
সর্বশক্তিমানতার প্রশ্নটি স্রষ্টার গুণাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি। এই বিষয়টি নিয়ে আস্তিক-নাস্তিক উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। নাস্তিকরা ‘পাথরের প্যারাডক্স’ দিয়ে প্রমাণ করতে চাই যে স্রষ্টা সর্বশক্তিমান নয়। স্রষ্টা কি এমন পাথর তৌরি করতে পারবে যা তিনি নিজেই তুলতে সক্ষম নন? যদি তিনি পারেন তাহলে তিনি আর সর্বশক্তিমান থাকেনা। কারণ এমন একটি জিনিস থাকে যা তিনি তুলতে সক্ষম নয়। আবার যদি তিনি না পারেন তাহলেও তিনি সর্বশক্তিমান নয়। কারণ এমন একটি জিনিস থাকে যা তিনি করতে পারেনা। যাইহোক, এই প্যারাডক্স নিয়ে আমরা পরবর্তী অংশে আলোচনা করবো। এখন স্রষ্টাকে কেন শক্তিমান হতে হবে এবং সেই শক্তিমান সত্তাকে কেন সর্বশক্তিমান হতে হবে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। সর্বশক্তিমান বলতে স্রষ্টার সর্বশক্তিমান গুণকে বোঝায়। স্রষ্টা সর্বশক্তিমান বলার অর্থ হল এই স্বীকৃতি দেওয়া যে তাঁর ক্ষমতার বাইরে কোন কিছুই নেই এবং কেউ তাঁর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। তিনি সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি এর সমস্ত ক্ষমতা রাখেন।
কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ‘Understanding omnipotence’ শিরোনামে প্রকাশিত একটি পেপারে সর্বশক্তিমান সত্তার সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে, একটি সর্বশক্তিমান সত্তা হবে এমন একটি সত্তা যার ক্ষমতা হলো সীমাহীন। মানুষের ক্ষমতা দুটি স্বতন্ত্র উপায়ে সীমাবদ্ধ; আমরা আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, এবং আমরা যা ইচ্ছা করেছি তা কার্যকর করার ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধতার এই দুটি স্বতন্ত্র উত্স সর্বশক্তিমানের একটি সহজ সংজ্ঞা প্রস্তাব করে; একজন সর্বশক্তিমান সত্তা হল এমন একজন যার ইচ্ছার নিখুঁত স্বাধীনতা এবং ইচ্ছার নিখুঁত কার্যকারিতা উভয়ই রয়েছে।[9]Kenneth L. Pearce and Alexander R. Pruss; Understanding omnipotence; Page: 403
এই সৃষ্টিজগতে আমরা যখন কোন সৃষ্ট বস্তু দেখি তখন স্বাভাবিকভাবে আমরা এটাই চিন্তা করি যে কোনো-না-কোনো শক্তিমান ও বুদ্ধিমান সত্তা এই বস্তুটিকে সৃষ্টি করেছে। যদি শক্তি না থাকে তাহলে কোনো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব না। কোন কিছু সৃষ্টি অথবা রুপান্তর করতে হলে ইচ্ছা শক্তি থাকা লাগবে। অর্থাৎ, কেউ যদি কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাই প্রথমে সেই বিষয়ে তার ইচ্ছা করা লাগবে। সেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে শক্তি থাকা লাগবে। সুতরাং, যেহেতু স্রষ্টা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন সেহেতু সৃষ্টি করতে হলে অবশ্যই শক্তির প্রয়োজন। তবে সৃষ্টিকর্তা শুধু শক্তিমান নয়, তিনি সর্বশক্তিমান। অর্থাৎ, তিনি এতোই শক্তিমান যার চাইতে শক্তিমান কোনো কিছুকে কল্পনা করা যায় না। সৃষ্টিকর্তা যদি সর্বশক্তিমান না হয় তাহলে তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে। তিনি চাইলে আরো শক্তি অর্জন করতে পারবেন এবং আমরা চাইলেই তার চেয়ে আরো বেশি শক্তিমান কোনো সত্তাকে চিন্তা করতে পারি। কোনো কিছুতে সীমাবদ্ধতা থাকলে তা পর-নির্ভরশীল হয়ে যায়। পর-নির্ভরশীল সত্তার অস্তিত্বের জন্য আবার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তা যদি পর-নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে তিনি কার উপর নির্ভরশীল? তিনি যার উপর নির্ভরশীল তিনিও কি পর-নির্ভরশীল? যদি তিনিও পর-নির্ভরশীল হয় তাহলে তার অস্তিত্বের জন্যও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এভাবে একের পর এক ব্যাখ্যা দিতে গেলে আমরা ইনফিনিটি রিগ্রেসে ঘটবে। সুতরাং, শুরুতে এমন একজন সত্তা থাকতে হবে যার চেয়ে শক্তিমান আর কেউ নেই। তাই অনিবার্য সত্তা বা অস্তিত্বকে অবশ্যই সর্বশক্তিমান হতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’আলা বলেন, “মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তত্ব ও রাজত্ব যার হাতে, তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান”।[10]সূরা আল-মুলক; ৬৭:১
স্রষ্টা প্রজ্ঞাবান
স্রষ্টার প্রজ্ঞাকে তাঁর জ্ঞানের সেই দিক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা এমন কিছুর প্রণয়ন করতে চায় যা স্রষ্টার করতে চাওয়া কাজের মধ্যে যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য রয়েছে তা বাস্তবায়ন করেন। ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়্যাহ জোর দিয়ে বলেছেন যে “ঈশ্বরের জ্ঞান যুক্তিযুক্ত এবং স্বজ্ঞাতভাবে (Intuitively) অনুমান করা যেতে পারে”।[11]Bassam Zawadi; A Critique of Deism; Page: 11
ইংরেজ দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক উইলিয়াম প্যালি এর মতে, “ঈশ্বরের বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞা তার সৃষ্টিতে আমরা যে জটিল নকশা লক্ষ্য করি তার মাধ্যমে অনুমানযোগ্য”।[12]Bassam Zawadi; A Critique of Deism; Page: 11
আমাদের এই সৃষ্টি জগতের জটিলতা আমাদের এটাই বলে যে এতো জটিল, সূক্ষ্মভাবে এই মহাবিশ্ব পরিচালনা করার জন্য অবশ্যই একজন জ্ঞানী, শক্তিমান ও সুনিপুণ কোন সত্তার প্রয়োজন। এই সৃষ্টিজগতে আমরা যখন কোন সৃষ্ট বস্তু দেখি তখন স্বাভাবিকভাবে আমরা এটাই চিন্তা করি যে আমাদের কোনো-না-কোনো বুদ্ধিমান সত্তা এই বস্তুটিকে সৃষ্টি করেছে। কেননা, আমাদের অভিজ্ঞতা, যুক্তি, আমাদের এটাই বলে যে, সৃষ্টিজগতের মধ্যে যত সুনিপুণ সৃষ্টি রয়েছে, তা সৃষ্টি করতে হলে ইলম বা জ্ঞান প্রয়োজন। আপনি যদি একটি চেয়ার তৈরি করেন, অথবা একটা টেবল তৈরি করেন, তৈরি করতে হলে প্রথমে আপনার চেয়ার সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং জ্ঞান থাকতে হলে অবশ্যই আপনাকে বুদ্ধিমান হতে হবে। এটা সম্ভব না যে একটা জড় বস্তু এসে চেয়ার তৌরি করবে অথচ তার পেছনে কোন বুদ্ধিমান সত্তার হাত নেই। সুতরাং, কোন বস্তু সৃষ্টি হলে সেই বস্তুর সৃষ্টিকর্তার অবশ্যই ইলম থাকা লাগবে এবং শক্তি থাকা লাগবে। স্রষ্টা যেহেতু আমাদের এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন সেহেতু স্রষ্টার অবশ্যই ইলম থাকা লাগবে। স্রষ্টার ইলম না থাকা অসম্ভব। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, “যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয়ে ভালোভাবে অবগত”। [13]সূরাঃ মুলক; ৬৭; ১৪
“সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না, জলে-স্থলে যা আছে তা তিনি জানেন, এমন একটা পাতাও পড়ে না যা তিনি জানেন না। যমীনের গহীন অন্ধকারে কোন শস্য দানা নেই, নেই কোন ভেজা ও শুকনো জিনিস যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) নেই”।[14]সূরা আল-আন আম; ৬;৫৯
“নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ”।[15]সূরা আল-বাকারা; ২:২৪৪
আল্লাহ তা’আলা সকল বস্তু সম্পর্কে অবশ্যই অবগত রয়েছেন, এ ব্যাপারে বিবেক বুদ্ধির দলিল হলো, বিনা ইলমে বস্তু সৃষ্টি করা আল্লাহ তা’আলার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি স্বীয় ইচ্ছার মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার ইচ্ছা করার জন্য উদ্দিষ্ট বস্তুর আকৃতি সম্পর্কে কল্পনা করা আবশ্যক। উদ্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে এ কল্পনার নাম ইলম। সুতরাং, সৃষ্টি করার জন্য ইচ্ছা করা জরুরি। আর ইচ্ছার জন্য ইলম আবশ্যক। একই সাথে সৃষ্টি করার জন্য ইলম থাকা জরুরি।[16]শারহুল আকীদাহ আত-তহাবীয়া; খন্ড নং; ১; পৃষ্টা ১৬৮-১৮৭ ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদ, ইবনে তাইমিয়া যুক্তি দেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টির সূক্ষ্মতা এবং নিপুণতা কেবল ঈশ্বরের জ্ঞানের উদাহরণ দেয় না বরং তার প্রতিটি সৃজনশীল কাজের অন্তর্নিহিত একটি উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক।[17]Bassam Zawadi; A Critique of Deism; Page: 11
স্রষ্টার প্রতিটি কাজ, বিশেষ করে মহাবিশ্ব সৃষ্টির মতো তাৎপর্যপূর্ণ কাজগুলোর একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য রয়েছে। স্রষ্টার স্বাধীন ইচ্ছা এবং প্রজ্ঞা উভয়ই আছে তা নিশ্চিত করার জন্য স্বীকার করা প্রয়োজন যে স্রষ্টার একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য কারণ বা উদ্দেশ্য থাকতে হবে যে কেন স্রষ্টা নির্দিষ্টভাবে একটা জিনিস সৃষ্টি করেছেন। মনে করুন আপনি একটি খেলনা গাড়ি তৈরি করলেন। কিন্তু আপনি কেন এটি তৈরি করেছেন? এর পেছনে অবশ্যই কোন কারণ বা উদ্দেশ্য রয়েছে। আপনিতো চাইলে খেলনা গাড়িটি নাও তৈরি করতে পারতেন বা খেলনা গাড়ির জায়গায় একটি খেলার বল তৈরি করতে পারতেন। তাহলে আপনি কেন খেলার বল তৈরি না করে খেলনার গাড়ি তৈরি করলেন? এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য থাকা লাগবে। যদি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি খেলার বল তৈরি না করে খেলনার গাড়ি তৈরি করার পেছনে যদি কোন কারণ বা উদ্দেশ্য থাকে তাহলে একজন নিখুঁত বা অত্যধিক জ্ঞানী স্রষ্টার সম্পর্কে কী বলা যায়? তিনি নিশ্চয়ই এই মহাবিশ্ব অকারণে বা উদ্দেশ্য ছাড়াই সৃষ্টি করেনি এবং কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই এই পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণ করেননি। তাই, এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণের পেছনে অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সাধন করার জন্য প্রজ্ঞাবান বা জ্ঞানী হওয়াটা আবশ্যক। কেননা, কোন জড় বস্তুর নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট লক্ষ বা উদ্দেশ্য থাকেনা এবং তা কোন কিছু সৃষ্টিও করতে পারেনা। স্রষ্টার প্রজ্ঞা হতে হবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের। অর্থাৎ, স্রষ্টা সর্বজ্ঞ বা সব জান্তা। স্রষ্টা সর্বজ্ঞ বলতে বুঝানো হয় যে সৃষ্টিকর্তা এমন জ্ঞানের অধিকারী যে তার চাইতে বেশি জ্ঞান আছে এমন কোনো সত্তা আর নেই। তার চাইতে জ্ঞানী আর কোনো সত্তাকে আমরা কল্পনা করতে পারিনা। স্রষ্টা যদি সর্বজ্ঞ না হয় তাহলে তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে। তিনি চাইলে আরো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। সুতরাং, তিনি নির্ভরশীল হয়ে যাবে কিন্তু স্রষ্টার সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটা সম্ভব না।
স্রষ্টা চিরন্তন
চিরন্তন সত্তা বলতে বুঝানো হয়, যিনি সর্বদা বিরাজমান। কোন সত্তা চিরন্তন না হওয়ার অর্থ হলো তার অস্তিত্বের শুরু আছে। অস্তিত্বের জন্য যার শুরু আছে তার অস্তিত্বের জন্য কারণ আছে। অর্থাৎ, সেই সত্তা তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নির্ভরশীল কোন সত্তা স্রষ্টা হতে পারে না। কারণ, নির্ভরশীল অস্তিত্বগুলো তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে এবং অস্তিত্বে আসার জন্য কার্যকারণ সম্পর্কও অসীম হতে পারে না। ইতিমধ্যে ‘কার্যকরণ সম্বন্ধ কি অসীম হতে পারে’ অংশে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেহেতু আমাদের এই মহাবিশ্ব পর-নির্ভরশীল এবং পর-নির্ভরশীল অস্তিত্বের জন্য ব্যাখ্যা বা কারণ প্রয়োজন, আর সেই ব্যাখ্যাটি অসীম সংখ্যক হতে পারবেনা, সেহেতু শুরুতে এমন একটা কারণ বা ব্যাখ্যা থাকা লাগবে যা কারণহীন কারণ, স্বাধীন, স্ব-নির্ভর, চিরন্তন, এবং অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল। যদি কারণ বা ব্যাখ্যাটি স্বাধীন, স্ব-নির্ভর, চিরন্তন, এবং অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল না হয় তাহলে ‘ইনফিনিটি রিগ্রেসে’ পতিত হবে।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা’আলা বলেন, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান”।[18]সূরা আলে-ইমরান; ৩;২
আয়াতে উল্লিখিত حَيّ শব্দের অর্থ চিরঞ্জীব।[19]https://www.almaany.com/quran/3/2/6/ قَيُّوم শব্দটি আল্লাহর আনাদিত্ব-সূচনাহীনতা এবং অবিনশ্বরতা-চিরন্তনতার প্রমাণ বহন করে। এটি আল্লাহ তা’আলার সর্বদা বিদ্যমান থাকা এবং পরিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা প্রমাণ করে। একই সাথে এই শব্দটি এই অর্থ বহন করে যে, আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা’আলা ওয়াজিবুল উজুদ (অনিবার্য অস্তিত্ব)।
স্রষ্টা কেন এক?
একটা দৃশ্যপট কল্পনা করুন যে, দুজন অনিবার্য সত্তা অস্তিত্বশীল। দুজনেরই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। আর সে কারণেই দুজনে দুই রকম ইচ্ছা করলো। অনিবার্য সত্তা-১ ইচ্ছা করলো পুরো মহাবিশ্ব কালো হবে। আর অনিবার্য সত্তা-২ ইচ্ছা করলো পুরো মহাবিশ্ব থাকবে সাদা। এখন দুজন অনিবার্য সত্তার ইচ্ছা কি প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব? অবশ্যই না! কারণ এটা যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিকতা তৈরি করে। এবার দৃশ্যপটটি ঠিক উল্টোভাবে চিন্তা করুন। দুইজনের একজনের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে অন্যজনের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়নি। এটা কি সম্ভব? যদি এটা সম্ভব হয় তাহলে যার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়নি সে অনিবার্য সত্তা হতে পারে না। কেননা, তার ইচ্ছা প্রতিফলিত করার ক্ষমতা বা শক্তি নেই। কিন্তু স্রষ্টা অবশ্যই সর্বশক্তিমান। সর্বশক্তিমান কোন সত্তা যদি তার ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে চাই তাহলে সেই ইচ্ছা প্রতিফলিত হবেই হবে। যার ইচ্ছা প্রতিফলিত হবেনা সে সর্বশক্তিমান নয়। কারণ তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে। তাই সে তার ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে পারেনি। অনিবার্য সত্তা-১ এর ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে কিন্তু অনিবার্য সত্তা-২ এর ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়নি। তাহলে অনিবার্য সত্তা-১ অনিবার্য সত্তা-২ এর চাইতে শক্তিমান। অনিবার্য সত্তা-১ শক্তিমান বিধায় তার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তিনিই হলে স্রষ্টা। সুতরাং, একই সাথে দুজন অনিবার্য সত্তা থাকা সম্ভব না। আরেকটি দৃশ্যপট কল্পনা করুন। দুজন অনিবার্য সত্তার কারো ইচ্ছাই প্রতিফলিত হলো না। অনিবার্য সত্তা-১ ইচ্ছা করলো মহাবিশ্ব সৃষ্টি করবে। অনিবার্য সত্তা-২ ইচ্ছা করলো মহাবিশ্ব সৃষ্টি করবে না। যদি দুইজন অনিবার্য সত্তার থাকে এবং সজ্ঞা অনুযায়ী তাদের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত হবে তাইলে কি মহাবিশ্ব আদৌ সৃষ্টি হতে পারতো? কার ইচ্ছাটা প্রতিফলিত হতো? দুজনের দুইরকম ইচ্ছাতো একই সাথে প্রতিফলিত হতে পারেনা। কারণ, এটা যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়ম বিরুধি। আর যদি একজনের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় তবে যার ইচ্ছা প্রতিফলিত হবে সেই হবে স্রষ্টা এবং যার ইচ্ছা প্রতিফলিত হবেনা সে নির্ভরশীল সত্তা। সুতরাং, অনিবার্য সত্তা হতে হবে একক। তিনি একক, সর্বশক্তিমান, এবং সর্বজ্ঞ। এই আর্গুমেন্টের মধ্যে পবিত্র কুরআনের সত্যতা ফুটে উঠেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়”।[20]সূরা ইখলাস; ১১২:১
স্রষ্টাই অনিবার্য অস্তিত্ব
অনিবার্য অস্তিত্ব বলতে বুঝায় কারণহীন কারণ, স্বাধীন, চিরন্তন, স্ব-নির্ভর অস্তিত্ব। মোডাল লজিক অনুসারে যে-সকল জিনিস বা অস্তিত্ব সকল সম্ভাব্য জগতে বাধ্যতামূলক বা অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল বা সত্য তাকে অনিবার্য অস্তিত্ব বলে। মুসলিম দার্শনিক ইবনে সিনা বলেন, “আমরা বলি যে প্রয়োজনীয় অস্তিত্ব (নেসেসারি এক্সিস্টেন্স) হলো অকারণ (অসৃষ্ট), যেখানে একটি ‘সামগ্রিক অস্তিত্ব'(নির্ভরশীল অস্তিত্ব) সৃষ্ট হয় এবং প্রয়োজনীয় অস্তিত্বটি (নেসেসারি এক্সিস্টেন্স) সমস্ত সম্ভাব্য উপায় এবং দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রয়োজনীয় (নেসেসারি)।[21] Mohammed Hijab; THE BURHĀN; Arguments for a Necessary Being Inspired by Islamic Thought; Page: 7
স্রষ্টার প্রকৃতি নিয়ে ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। স্রষ্টা এমন এক সত্তা যিনি স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল বা স্ব-নির্ভর, অস্তিত্বের জন্য তিনি কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, যিনি চিরন্তন সত্তা, তার অস্তিত্ব না থাকা সম্ভব নয়, যিনি হবে একক সত্তা। অনিবার্য অস্তিত্বও এমন সত্তা যিনি স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল বা স্ব-নির্ভর, অস্তিত্বের জন্য তিনি অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, তিনি চিরন্তন, তার অনস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল বা স্ব-নির্ভর, অস্তিত্বের জন্য তিনি অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, তিনি চিরন্তন, তার অনস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়, যিনি হবে একক সত্তা, এই বৈশিষ্ঠ্যগুলি একমাত্র স্রষ্টার প্রকৃতির সাথেই খাপ খায়। সুতরাং, অনিবার্য অস্তিত্বই মূলত স্রষ্টা এবং এই যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ হয়।
References
| ↑1 | Mohammed Hijab; THE BURHĀN; Arguments for a Necessary Being Inspired by Islamic Thought; Page: 7 |
|---|---|
| ↑2 | Alexander R. Pruss and Joshua L. Rasmussen; Necessary Existence; Page: 4 |
| ↑3 | যুক্তিবিদ্যা কি ? – Faith and Theology (faith-and-theology.com) |
| ↑4 | Protection and Dosimetry an Introduction to Health Physics. https://doi.org/10.1007/978-0-387-49983-3 |
| ↑5 | Caslav Brukner Causality in a quantum world. DOI.org/10.1063/PT.6.1.20180328a |
| ↑6 | D’Ariano, G. M. (2018). Causality re-established. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 376(2123), 20170313 |
| ↑7 | Physics – The Force of Empty Space (aps.org) |
| ↑8 | সূরা ইখলাস; ১১২: ১-৪ |
| ↑9 | Kenneth L. Pearce and Alexander R. Pruss; Understanding omnipotence; Page: 403 |
| ↑10 | সূরা আল-মুলক; ৬৭:১ |
| ↑11, ↑12, ↑17 | Bassam Zawadi; A Critique of Deism; Page: 11 |
| ↑13 | সূরাঃ মুলক; ৬৭; ১৪ |
| ↑14 | সূরা আল-আন আম; ৬;৫৯ |
| ↑15 | সূরা আল-বাকারা; ২:২৪৪ |
| ↑16 | শারহুল আকীদাহ আত-তহাবীয়া; খন্ড নং; ১; পৃষ্টা ১৬৮-১৮৭ |
| ↑18 | সূরা আলে-ইমরান; ৩;২ |
| ↑19 | https://www.almaany.com/quran/3/2/6/ |
| ↑20 | সূরা ইখলাস; ১১২:১ |
| ↑21 | Mohammed Hijab; THE BURHĀN; Arguments for a Necessary Being Inspired by Islamic Thought; Page: 7 |
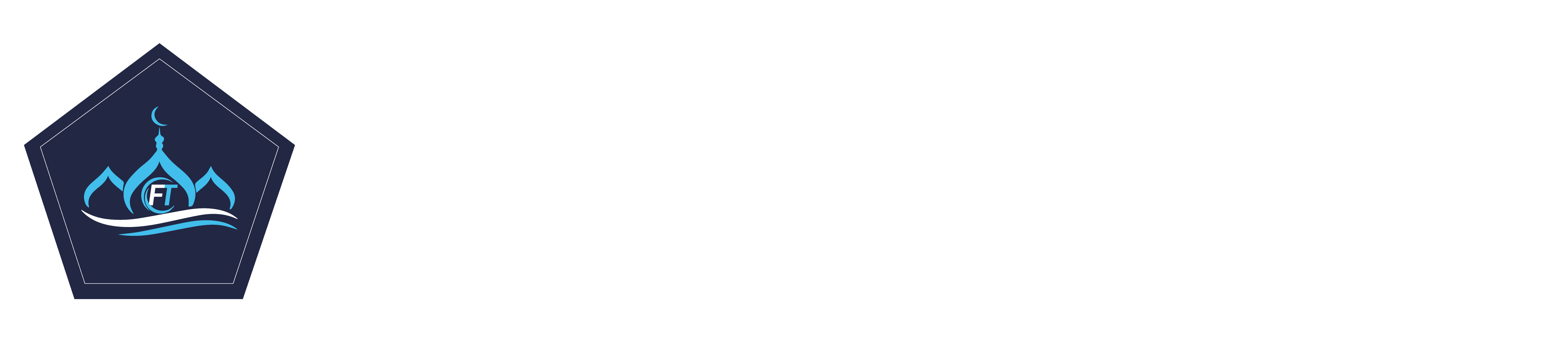
5 Comments